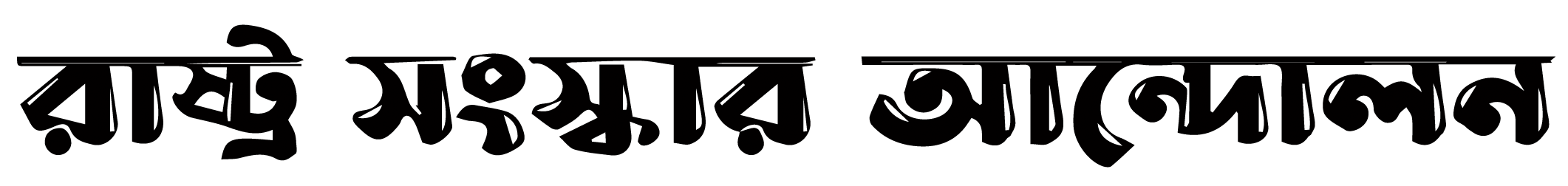তৃতীয় অংশের পর...
সংবিধানের দশমভাগ সংবিধান সংশোধন সংক্রান্ত। এ ভাগে একটিই অনুচ্ছেদ ১৪২। যাতে বলা আছে: এই সংবিধানে যাহা বলা আছে তাহা সত্তে¡ও সংসদের আইন-দ্বারা এই সংবিধানের কোনো বিধান সংশোধিত বা রহিত হইতে পারিবে। এ জন্য প্রয়োজন হবে তিনভাগের দুইভাগ সংসদ সদস্যের অনুমোদন।
এ সামান্য বিধানটুকুর কী অসামান্য ক্ষমতা, তা চতুর্থ সংশোধনী বা পঞ্চদশ সংশোধনী পড়ে না দেখলে শুধু দশম অধ্যায় পড়ে, এমনকি কল্পনা করাও সম্ভব নয়।
সংসদ সদস্যদের দুই-তৃতীয়াংশ যদি একমত হয়, তাহলে লাখ লাখ মানুষের জীবনদান, দুই লাখ নারীর মর্যাদাহানি, দুই কোটি মানুষের দেশত্যাগ আর অজস্র মানুষের দীর্ঘ লড়াই সংগ্রামের মধ্যদিয়ে যে রাষ্ট্রটি গড়ে উঠেছে, যে রাষ্ট্র হয়ে উঠার অঙ্গীকার ব্যক্ত করেছে সংবিধান, তা অবলীলায় এক অধিবেশনে মাত্র কয়েক মিনিটের সিদ্ধান্তে আমূল বদলে দেয়ার সুযোগও রেখেছে। আর এ বদলে ফেলাকে অবৈধ বা বেআইনিও বলা যাবে না। এত বড় অগণতান্ত্রিকতার দৈত্যটিকে সংবিধানের বুকের মধ্যে সযতেœ পুষে রেখে এই সংবিধানকে গণতান্ত্রিক সংবিধান হিসাবে যারা দাবি করেন, তারা হয়তো দুই-তৃতীয়াংশ সংসদ সদস্যের ইচ্ছা-অনিচ্ছাকেই গণতন্ত্র মনে করেন। আরো পরিষ্কারভাবে বললে তারা হয়তো সেই প্রধানমন্ত্রীর ইচ্ছা-অনিচ্ছা আর গণতন্ত্রের মধ্যে কোনো পার্থক্য দেখেন না, যার দল দুই-তৃতীয়াংশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা নিয়ে সরকার গঠন করেছে।
বিবিধ বিধিবিধান
সংবিধানের একাদশ ভাগ হলো-বিবিধ। এই ভাগে প্রজাতন্ত্রের সম্পত্তি, প্রজাতন্ত্রের নির্বাহী বিভাগের চুক্তি প্রণয়নের ক্ষমতা, প্রচলিত আইনের হেফাজত, সংবিধান প্রণেতাদের বিবেচনায় এমন কিছু ছোটখাটো বিষয়ের বিধিবিধান লিপিবদ্ধ করা হয়েছে।
এই ভাগের বর্ণিত ক্ষমতাকে একটু পরিষ্কার করে বোঝার জন্য দুটি উদাহরণ দেয়া যেতে পারে: (১) অনুচ্ছেদ ১৪৪-এ বলা হয়েছে “প্রজাতন্ত্রের নির্বাহী কর্তৃত্বে-সম্পত্তি গ্রহণ, বিক্রয়, হস্তান্তর, বন্ধক, দান ও বিলি ব্যবস্থা, যে কোনো কারবার বা ব্যবসায় চালনা এবং যে কোনো চুক্তি প্রণয়ন করা যাইবে।”
সংবিধানের এই অনুচ্ছেদে স্পষ্টভাবে দেখা এবং বোঝার জন্য ১৯৭৪ সালের ১৬ মে পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হয়েছে। এই দিন দিল্লিতে বাংলাদেশ ও ভারতের মধ্যে যে সীমান্ত চুক্তি হয়, যা ‘বেরুবাড়ি চুক্তি’ হিসাবেই বেশি পরিচিত, তা সম্পন্ন হওয়ার পর অবশ্য স্পষ্টভাবে বোঝা গেছে যে, ‘চুক্তি’ মানে এমন কোনো আন্তর্জাতিক চুক্তি যা দেশের সীমানা পর্যন্ত পুনঃনির্ধারণ করে দিতে পারে এবং এই ধরনের কোনো চুক্তি করার জন্য সংসদে ন্যূনতম কোনো আলোচনার কোনো বাধ্যবাধকতা ’৭২-এর সংবিধান রাখেনি।
(২) ১৪৩ অনুচ্ছেদে তেল-গ্যাস-খনিজকে জনগণের সম্পদ হিসাবে ঘোষণা করা হয়েছে। সেই সম্পদ নিয়ে কায়-কারবার, চুক্তি সবই করার ক্ষমতা সংবিধান সরকারকে দিয়ে রেখেছে এবং এরই ধারাবাহিকতায় তেল-গ্যাস, ট্রানজিট যা কিছু চুক্তিই সরকার করুক না কেন, তার জন্য কোনো আলোচনা পর্যন্ত কোথাও করার প্রয়োজন ’৭২-এর সংবিধান অনুযায়ী নাই।
প্রায় অনুল্লেখ্য একটি অনুচ্ছেদ ১৪৯
সংবিধানের প্রায় শেষ দিকে একাদশ ভাগের বিবিধ অধ্যায়ের একটি প্রায় অনুল্লেখ্য অনুচ্ছেদ ১৪৯ বলা হয়েছে “এই সংবিধানের বিধানাবলী সাপেক্ষে সকল প্রচলিত আইনের কার্যকারিতা অব্যাহত থাকবে, তবে অনুরূপ আইন এই সংবিধানের অধীন প্রণীত আইনের দ্বারা সংশোধিত বা রহিত হইতে পারিবে।”
অনুচ্ছেদ ১৫২-তে অন্যান্য সংজ্ঞার সঙ্গে ‘আইন’ এবং ‘প্রচলিত আইন’-এর সংজ্ঞা দেয়া হয়েছে এইভাবেÑ‘আইন’ অর্থ কোনো আইন, অধ্যাদেশ, আদেশ, বিধি, প্রবিধান, উপ-আইন, বিজ্ঞপ্তি ও অন্যান্য আইনগত দলিল এবং বাংলাদেশে আইনের ক্ষমতাসম্পন্ন যে কোনো প্রথা বা রীতি।
‘প্রচলিত আইন’ অর্থ: “এই সংবিধান-প্রবর্তনের অব্যবহিত পূর্বে বাংলাদেশের রাষ্ট্রীয় সীমানায় বা উহার অংশ বিশেষে আইনের ক্ষমতাসম্পন্ন কিন্তু কার্যক্ষেত্রে সক্রিয় থাকুক বা না থাকুক, এমন যে কোনো আইন।” যার অর্থ হলো, ২৬ মার্চের স্বাধীনতা ঘোষণার পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত যে সমস্ত আইন এদেশে জারি ছিল, কার্যক্ষেত্রে তা সক্রিয় থাকুক বা না থাকুক, স্বাধীনতার পর ’৭২-এর সংবিধান গৃহীত হওয়ার পরও সে সবই আইন হিসাবে বহাল থাকবে। যা ছিল পাকিস্তানে, যা ছিল ব্রিটিশের, যাকে বলা হয়েছে ঔপনিবেশিক, যাকে বলা হয়েছে গণবিরোধী, তার সবই বহাল রেখে আশ্চর্যজনকভাবে সংবিধানকে প্রচলিত আইনের অধীনস্থ করা হয়েছে। প্রচলিত আইনকে সংবিধানের অধীনস্থ করা হয়নি। অনুচ্ছেদ ৭(২) যত উচ্চকণ্ঠেই ঘোষণা করুক না কেন “এই সংবিধান প্রজাতন্ত্রের সর্বোচ্চ আইন” কার্যত তা চাতুরিপূর্ণ, মিথ্যা এবং জোচ্চুরি ছাড়া আর কিছুই নয়। যা ছিল ব্রিটিশবিরোধী আন্দোলনের মূলমন্ত্র, যে আকাঙ্খায় মানুষ ২৩ বছর লড়াই করেছে পাকিস্তান সরকারের বিরুদ্ধে, যে সমাজ গড়বে বলে সশস্ত্র যুদ্ধে জীবন দিয়েছে এদেশের কৃষক-শ্রমিক-মেহনতি মানুষ, সেই আকাক্সক্ষাগুলো সুন্দর করে লিখে সংবিধানে লটকে দিয়ে বলা হলো: এই তোমাদের আকাঙ্খিত রাষ্ট্র, এ রাষ্ট্র তোমাকে মুক্তি দেবে। আর কার্যক্ষেত্রে এইসব আকাঙ্খার বিপরীতে প্রচলিত আইন, বিদ্যমান আইন, আর নতুন নতুন আইনপ্রণয়ন করে একটি অমানবিক, নৃশংস, স্বৈরাচারী রাষ্ট্র তৈরি করা হয়েছে। স্বাধীনতার মাত্র এক বছরের মধ্যে একটি দেশকে কিভাবে পুনরায় পাকিস্তানের স্বৈরাচারী কাঠামোতে ঢুকিয়ে দেয়া হলো তা আজ ভাবলেও বিস্মিত হতে হয়।
স্বাধীনতা লাভের মাত্র ১০ মাসের মধ্যে একটি সংবিধান প্রণয়ন ও প্রবর্তন করতে পারা আগেই উল্লেখ করা হয়েছে ইতিহাসে বিরল; কিন্তু তার চাইতেও বিরল, রক্তের দাগ শুকানোর আগে, ধর্ষিতাদের হাহাকার বাতাস থেকে মিলিয়ে যাওয়ার আগে, পোড়াবাড়ি-পোড়াঘর রাস্তা-ঘাট চলার মতো সংস্কার হওয়ার আগেই-কিভাবে বাংলাদেশকে আবার পাকিস্তান বানিয়ে ফেলা গেল। সংবিধানের ১৪৯ অনুচ্ছেদ সেই অসাধ্যই সাধন করেছে-সরাসরি, কোনো রাখঢাক ছাড়া, কোনো অঙ্গীকার বা প্রতিশ্রুতি পর্যন্ত না দিয়ে। বিষয়টি একটু পরিষ্কার করার জন্য একটি সাধারণ উদাহরণ দেয়া যেতে পারে।
পুলিশের গুলিতে মৃত্যু
অনুচ্ছেদ ১৪৯ অনুযায়ী আইন ও সংবিধানসম্মত
পূর্বেই আমরা দেখেছি, সংবিধানের ১৪৯ নং অনুচ্ছেদ অনুযায়ী সংবিধান গৃহীত হওয়ার অব্যবহিত পূর্বে যে সকল আইন তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানে বিদ্যমান ছিল, কার্যক্ষেত্রে তা সক্রিয় থাকুক বা না থাকুক, তার সবকিছুরই কার্যকারিতা অব্যাহত থাকবে। সে অনুযায়ী পূর্বে উল্লেখিত ১৮৯৮ সালে ব্রিটিশ প্রবর্তিত ফৌজদারি কার্যবিধির কার্যকারিতা আজ অবধি অব্যাহত আছে।
সেই ফৌজদারি কার্যবিধির ৪৬ ধারায় কোনো আসামিকে গ্রেপ্তার নিশ্চিত করার জন্য পুলিশ কি কি করতে পারবে, তার একটি বিবরণ দেয়া আছে।
ধারা ৪৬(৩)-এ বলা হয়েছে “এই ধারার কোনোকিছুই কোনো মানুষকে হত্যার অধিকার দেয় না। যদি সে মৃত্যুদন্ড বা যাবজ্জীবন কারাদন্ডে দন্ডিত হতে পারে এমন কোনো অপরাধের অভিযোগে অভিযুক্ত না হয়।” আইনটি সাধারণ বাংলায় লিখলে লেখা যায়: কোনো আসামি যদি যাবজ্জীবন কারাদন্ড বা মৃত্যুদন্ডে দন্ডিত হতে পারে এমন অপরাধ সংগঠনের অভিযোগে অভিযুক্ত হয় তাহলে, পুলিশ তার গ্রেপ্তার নিশ্চিত করার জন্য এমন পদপেক্ষ নিতে পারে যাতে সে নিহত হতে পারে।
ব্রিটিশরা অবশ্য ‘সভ্য জাতি’। তাই কোনো হত্যাকান্ড ই বিনা তদন্তে মেনে নিতে রাজি নয়। তাই পুলিশ রেগুলেশন ১৮৬১-র ১৫৭ নং রেগুলেশনে, গোলাগুলির ঘটনা ঘটলে তার প্রশাসনিক তদন্তের ব্যবস্থা রেখেছে। প্রশাসনিক তদন্তে যদি দেখা যায় যে, পুলিশদের গুলি ছোড়াটা যথার্থ তাহলে আর কোনো সমস্যা নাই।
আমাদের যেসব বন্ধু সংবিধান পড়েছেন যারা জানেন যে, ’৭২-এর সংবিধানের মৌলিক অধিকার অধ্যায়ে বর্ণিত ‘জীবন ও ব্যক্তি স্বাধীনতার অধিকার’ মৌলিক অধিকার। তারা আরো জানেন, যেসব আইন মৌলিক অধিকারের সঙ্গে অসামঞ্জস্যপূর্ণ সেগুলো বাতিল হয়ে যাবে। তাদের কাছে মনে হতে পারে পুলিশের গুলি করে মানুষ মারা মৌলিক অধিকার পরিপন্থী এবং এ আইন বাতিল হওয়াই সংবিধানসম্মত। সেসব বন্ধুরা যদি অনুচ্ছেদ ৩২ একটু মনোযোগ দিয়ে পড়েন, যেখানে বলা হয়েছে “আইনানুযায়ী ব্যতীত জীবন ও ব্যক্তি স্বাধীনতা হইতে কোনো ব্যক্তিকে বঞ্চিত করা যাইবে না’’ সেখানে ‘আইনানুযায়ী’ শব্দটিতে একটু মনসংযোগ করতে হবে এবং করলেই দেখা যাবে এ অধিকারটিও নিরঙ্কুশ নয়। ফৌজদারি কার্যবিধির ৪৬(৩) ধারার আড়ালে থেকে যদি পুলিশ গুলি করে কাউকে খুন করে আর তা যদি প্রশাসনিক তদন্তে যথার্থ বলে প্রতীয়মান হয়, তবে তা হবে আইনের প্রতিপালন মাত্র।
আজকাল যে হরহামেশাই ক্রসফায়ারের গল্প আমরা দেখি এবং এতদসংক্রান্ত যেসব প্রেসনোট পত্রিকায় জনগণের উদ্দেশ্যে প্রকাশিত হয় তার সবকিছুরই আইনগত ভিত্তিটি কিন্তু সংবিধানেই রয়েছে। আর ’৭২-এর সংবিধান ও সেই হত্যাকাÐের অনুমোদনকারী ‘পবিত্র দলিল’ হিসাবে আমাদের মতো নিশ্চুপ বসে থাকে। আগেও বলা হয়েছে, পৌনঃপুনিকতার ঝুঁকি নিয়েই আবারো বলা যায়, যেসব অধিকারকে সাধারণভাবে সংবিধান পাঠ করে মৌলিক অধিকার হিসাবে বিবেচনা করে নাগরিকগণ আত্মতুষ্টিতে ভুগেন, তারা একটু সতর্ক চোখে পড়লেই দেখবেন, যতগুলো মৌলিক অধিকার রয়েছে; হোক তা সংগঠন সমাবেশ করার স্বাধীনতা বা চিন্তা বা মতপ্রকাশের স্বাধীনতা, তার প্রত্যেকটি অনুচ্ছেদেই কিছু আপাত নিরীহ শব্দবন্ধ রয়েছে-যেমন, “আইনানুযায়ী” বা “আইনের দ্বারা আরোপিত বাধানিষেধ সাপেক্ষে”, অথবা “জনস্বার্থ ”, “নৈতিকতা” বা “শৃঙ্খলা রক্ষার জন্য প্রয়োজনীয় বাধানিষেধ” সাপেক্ষে-এসব অধিকারকে মৌলিক অধিকার হিসাবে স্বীকৃতি দেয়া হয়েছে। আর এই আইনের সবগুলো হোক তা ফৌজদারি কার্যবিধি, দন্ডবিধি, পুলিশ রেগুলেশন বা অন্যকিছু তার সবই ব্রিটিশরা তৈরি করেছিল এখানকার জনগণকে শাসন আর আন্দোলনকারীদের দমন-পীড়নের জন্য, যা অব্যাহত রেখেছিল পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠী, যা ছিল পাকিস্তানে, বাংলাদেশেও সেটা হুবহু কার্যকর আছে।
এখানে প্রসঙ্গক্রমে আর একটি কথা বলা প্রয়োজন, তাহলো এই সংবিধানের প্রণেতা বলে দাবিদারদের কেউ কেউ এখনো পর্যন্ত এভাবে বিভ্রান্তি ছড়ানোর চেষ্টা করে থাকেন যে, ‘দেশ সংবিধান অনুযায়ী চলছে না’ বা ‘দেশে আইনের শাসন নাই’। আমাদের অনেক পন্ডিত বুদ্ধিজীবী আইনগুলোকে যথাযথ পর্যালোচনা বা পর্যবেক্ষণ না করেই হরহামেশা বলে থাকেন আমাদের আইনের কোনো অভাব নাই, আমাদের সব বিষয়ে আইন আছে, শুধু আইনের যথাযথ প্রয়োগ হয় না। সেসব পন্ডিত-প্রণেতাদের খুব বিনয়ের সঙ্গে বোধহয় এটা মনে করিয়ে দেয়ার প্রয়োজন আছে যে, আইন যদি গণবিরোধী হয়, আইন যদি লুটেরাদের হয়, সংবিধান যদি সেইসব আইনের পৃষ্ঠপোষকতা করে তবে দেশে তথাকথিত ‘আইনের শাসন’ যত প্রতিষ্ঠিত হবে, দেশ যতবেশি সংবিধান অনুযায়ী চলবে ততবেশি দেশের নিরপরাধ, সাধারণ শ্রমজীবী নির্দোষ মানুষ আইনি নির্যাতনের শিকার হবে। আর তার বিপরীতে লুটেরা, খুনি, প্রকৃত সন্ত্রাসীরা রাষ্ট্রীয় ও আইনি মদতে বড় থেকে আরো বড় সম্পদশালী, ক্ষমতাশালী, ধরাছোঁয়ার বাইরের দানবে পরিণত হবে। এ প্রক্রিয়া ব্রিটিশ আমলে ছিল, পাকিস্তানেও ছিল, বাংলাদেশে অত্যন্ত নতুন কৌশলে বহাল করা হয়েছে। ’৭২-এর সংবিধান তার সবচেয়ে বড় হাতিয়ার হিসাবে কাজ করছে।
সংবিধানে ‘বিবিধ’ অধ্যায়ের শেষে চারটি তফসিল যুক্ত করা হয়েছে। প্রথম তফসিলটি ‘মৌলিক অধিকার অধ্যায়’-এর ৪৭ নং অনুচ্ছেদের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত। এ অনুচ্ছেদে বলা হয়েছিল ‘রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতি’ অংশের কোনো অঙ্গীকার পূরণ করতে যেয়ে যদি কোনো বিধান করা হয়, তবে তা মৌলিক অধিকার পরিপন্থী হলেও বাতিল হবে না।
প্রাথমিকভাবে এই অনুচ্ছেদ এবং প্রথম তফসিলের উল্লিখিত আইনসমূহ পাঠ করলে একে সমাজতন্ত্র অভিমুখী মনে হতে পারে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এ ছিল তথাকথিত জাতীয়করণ অভিমুখী, তার চেয়েও বড় বিষয় হলো, এ আইনে তিনভাগের দুই ভাগ সংসদ সদস্যের সম্মতিতে রাষ্ট্রের ক্ষতিপূরণ দেয়ার বিধান করার ব্যবস্থা উন্মুক্ত রাখা হয়েছিল।
দ্বিতীয় তফসিলটি মূলত সংবিধানের ৪৮ অনুচ্ছেদ বর্ণিত রাষ্ট্রপতি নির্বাচনসংক্রান্ত বিধিবিধান সম্বলিত; আর তৃতীয় তফসিলে, রাষ্ট্রপতি প্রধানমন্ত্রী এবং অপরাপর মন্ত্রী, স্পীকার, ডেপুটি স্পীকার, সংসদ সদস্য, প্রধান বিচারপতি বা অন্যান্য বিচারক, প্রধান নির্বাচন কমিশনার-সহ অপরাপর কমিশনার, মহা হিসাব-নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রক, সরকারি কর্মকমিশনের সদস্যদের বিভিন্ন প্রকার শপথনামা লিপিবদ্ধ আছে।
তফসিলসমূহের মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ তফসিলটি হলো চতুর্থ তফসিল। সংবিধানের ১৫০ অনুচ্ছেদে “এই সংবিধানের অন্য কোনো বিধান সত্তে¡ও চতুর্থ তফসিলে বর্ণিত ক্রান্তিকালীন ও অস্থায়ী বিধানাবলী কার্যকর হইবে” বলে যে বিধানাবলীর উল্লেখ করা হয়েছে, তার বিবরণ দেয়া আছে।
এসব বিবরণীর মধ্যে প্রথমেই, সংবিধান প্রবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে গণপরিষদ ভেঙ্গে যাওয়ার ঘোষণা দেয়া হয়। দ্বিতীয়ত, যতশীঘ্র সম্ভব সংসদ সদস্য নির্বাচন অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা নেয়ার অঙ্গীকার ব্যক্ত করা হয় এবং বলা ভালো, সংবিধান প্রবর্তনের পূর্বের নির্বাচন কমিশনকেই সংবিধান অনুযায়ী প্রতিষ্ঠিত নির্বাচন কমিশন হিসাবে গণ্য করা হয়। একইভাবে সংবিধান প্রণয়নের পূর্বের প্রধান বিচারপতি এবং বিচারকগণকে সংবিধানের ৯৫ অনুচ্ছেদ অনুযায়ী নিযুক্ত প্রধান বিচারপতি ও বিচারক হিসাবে গণ্য করার বিধান রাখা হয়। অনুরূপ ব্যবস্থা করা হয় সরকারি কর্মকমিশন এবং সরকারি কর্মক্ষেত্রের বেলায়। যেসব কর্মকর্তা-নির্বাহী বিভাগ ও বিচার বিভাগীয় কর্তৃপক্ষের কর্মচারী যে যেই অবস্থায় ছিলেন, সে সেই অবস্থানে থেকেই স্ব স্ব দায়িত্ব পালন করবেন বলে বিধান জারি করা হয়।
এই তফসিলের বিধান অনুযায়ী, ইতিপূর্বে ‘বাংলাদেশ’ নামক রাষ্ট্রটি যে কেবল পাকিস্তান ও ব্রিটিশ আইনকানুন নিয়ে যাত্রা শুরু করেছিল তাই নয়, তার সঙ্গে এইটুকুও যুক্ত করতে হবে যে-বাংলাদেশ রাষ্ট্রটি পাকিস্তানী আইন-কানুন, সেইসব আইন-কানুনের পৃষ্ঠপোষকদের নিয়েও (যে যেইখানে যে অবস্থায় ছিলেন তাদেরকে সেই সেই অবস্থানে রেখেই) পথচলা শুরু করে।
বলাবাহুল্য, ইতিপূর্বে স্বাধীনতা ঘোষণার সঙ্গে সঙ্গেই, মানে ১০ এপ্রিল তারিখে 'Law Continuence Enforcement Order'-এর মাধ্যমে শুধু ২৪ মার্চ পূর্ববর্তী আইন-কানুনগুলোকে বহাল রাখা হয়নি, ঘোষণায় এ-ও বলা ছিল, সরকারী কর্মকর্তাগণ যে যেই সার্ভিসে ছিলেন, যথা: সিভিল, মিলিটারি, জুডিশিয়াল, ডিপ্লোম্যাট, সবাই সে-ই সে-ই অবস্থানে বহাল থাকবে, যদি তারা বাংলাদেশ সরকারের প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করেন।” পরবর্তীকালে আনুগত্যের শর্তটিও আর যুক্ত রাখা হয়নি।
বহুল আলোচিত বিষয়গুলো সম্পর্কে
বাংলাদেশের সংবিধান নিয়ে আমাদের দেশে যেসব আলোচনা সচরাচর হয়ে থাকে তার একটি বড় অংশ জুড়ে থাকে জাতীয়তাবাদ আর ধর্মনিরপেক্ষতার প্রশ্ন। নারী প্রশ্নেও ইদানীং বিভিন্ন আলোচনা উত্থাপিত হতে দেখা যায়। এ বিষয়গুলো আমরা এখানে বিস্তারিত আলোচনা করতে চাই না। তবে এটি খুব আশ্চর্যজনক ও বিস্ময়কর মনে হয় যে, বাঙালিরা স্বাধীনতার মাত্র ১০ মাসের মাথায় যে সংবিধানটি প্রণয়ন ও গ্রহণ করলো তা কিভাবে এতটা জাতিবিদ্বেষী হতে পেরেছিল।
একথা প্রায় সবার জানা যে, তৎকালীন পূর্ব-পাকিস্তানের জনগণ, পশ্চিম পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠীর জাতিগত নিপীড়নের শিকার হতে হতে নিজেদের জাতিগত স্বকীয়তার ও আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকারের যে লড়াই শুরু করে তা এক পর্যায়ে তাদের সশস্ত্র যুদ্ধে নামতে বাধ্য করে। আমরা দাবি করি আমাদের প্রায় ৩০ লক্ষ শহীদ, দুই লক্ষ মা-বোনের ইজ্জত আর দুইকোটি মানুষের দেশ ছাড়া হতে হয়েছিল পাকিস্তানি শাসক গোষ্ঠীর নিপীড়নে। এরকম একটি বীভৎস অভিজ্ঞতার যারা শিকার তারা স্বাধীনতার মাত্র ১০ মাসের মাথায় কিভাবে এমন সংবিধান গ্রহণ করে যেখানে অপরাপর জাতিসত্তার স্বীকৃতি পর্যন্ত দেয়া হলো না!
সংবিধানের ২৩ নং অনুচ্ছেদে ‘জাতীয় সংস্কৃতি’ প্রশ্নে বলা হয়, জাতীয় ভাষা, সাহিত্য ও শিল্পকলাসমূহের পৃষ্ঠপোষণের ব্যবস্থা করবে রাষ্ট্র। উপরোক্ত অনুচ্ছেদসমূহ থেকে শুরু করে গোটা সংবিধান পাঠ করে কারো পক্ষে বোঝার ক্ষমতা নাই যে, এদেশে বাঙালিদের বাইরে অপর কোনো জাতিগোষ্ঠীর অস্তিত্ব আছে।
এইসব জনগোষ্ঠীকে শুধুমাত্র যে জাতিগত স্বীকৃতি দেয়া থেকে বঞ্চিত রাখা হয়েছে তা নয়, সংবিধান তার মূলনীতি অধ্যায়ের ( যা বাস্তবায়নে রাষ্ট্রকে বাধ্য করা যায় না) ১৩নং অনুচ্ছেদে মালিকানার যেসব ধরন নির্দিষ্ট করেছে যথা: রাষ্ট্রীয় মালিকানা, সমবায়ী মালিকানা এবং ব্যক্তিগত মালিকানা, তা অত্যন্ত সুকৌশলে এইসব জনগোষ্ঠী যে ধরনের মালিকানা চর্চ্চায় অভ্যস্ত সেই “যৌথ মালিকানা”র ধারণাকেই বিলুপ্ত করে দিয়েছে। বর্তমানে এইসব জনগোষ্ঠীকে সংবিধান স্বীকৃত মালিকানা নীতির ভিত্তিতেই তাদের ভূমি সমস্যার সমাধান করতে চাপ দেওয়া হচ্ছে ।
আমাদের সংবিধানের দ্বিতীয় ভাগ, যার শিরোনাম ‘রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতি’ সেই ভাগের ২২ নং অনুচ্ছেদে ধর্মনিরপেক্ষতার প্রশ্নটি প্রথম উত্থাপন করা হয়। একটু লক্ষ করলে পাঠক দেখতে পাবেন, এ অনুচ্ছেদের শিরোনামটি ‘ধর্মীয় স্বাধীনতা’-র সঙ্গে যুক্তভাবে উপস্থাপন করা হয়েছে। ধর্মনিরপেক্ষতা ও ধর্মীয় স্বাধীনতা হিসাবে বলা হয়েছে, ধর্ম নিরপেক্ষতার নীতি বাস্তবায়নের জন্য, সকল প্রকার সা¤প্রদায়িকতা, কোনো ধর্মকে রাজনৈতিক মর্যাদাদান, ধর্মের রাজনৈতিক অপব্যবহার এবং কোনো বিশেষ ধর্ম পালনকারীদের প্রতি বৈষম্য বা নিপীড়ন রাষ্ট্র বিলোপ করবে।
সংবিধানের তৃতীয় ভাগের মৌলিক অধিকার অংশের অনুচ্ছেদ ২৮এ ‘ধর্ম প্রভৃতি কারণে বৈষম্য না করার বিধান জারি রয়েছে’। এ অনুচ্ছেদে ধর্মের প্রশ্নের সঙ্গে নারীর প্রশ্নটিকে জুড়ে দেয়া হয়েছে এইভাবে “কেবল ধর্ম, গোষ্ঠী, বর্ণ, নারী-পুরুষভেদ বা জন্মস্থানের কারণে কোন নাগরিকের প্রতি রাষ্ট্র বৈষম্য প্রদর্শন করিবে না” এবং “রাষ্ট্র ও গণজীবনের সর্বস্তরে নারী-পুরুষের সমান অধিকার লাভ নিশ্চিত করিবেন।” শিক্ষায়-চাকরি ইত্যাদিতে নারী-পুরুষ ভেদের জন্য কোনো বৈষম্য রাষ্ট্র করবে না বলেও ঘোষণা করা হয়েছে।
প্রশ্ন হলো, নারী-পুরুষ ভেদে রাষ্ট্র সকলের প্রতি সমান আচরণ করার জন্য অঙ্গীকারাবদ্ধ থাকার পরেও মুসলিম নারী কেন সম্পত্তিতে ভাইয়ের সমান অংশ পায় না বা হিন্দু ও বৌদ্ধ নারীকে কেন কোনো উত্তরাধিকারই রাষ্ট্র দিতে পারে না তার জবাব পাওয়ার জন্য পুনর্বার মুসলিম আইন ও হিন্দু-বৌদ্ধ আইন যে ‘আইন’ এবং তা যে সংবিধান প্রণয়নের অব্যবহিত পূর্বে যেভাবে বহাল ছিল, সেভাবেই এখনও বহাল আছে তার জন্য সংবিধানের ১৪৯ অনুচ্ছেদ পুনরায় দেখে নিতে হবে। আর সেটা নিলেই জানা যাবে, সংবিধান নারীর জন্য যত কথাই বলুক না কেন শেষ পর্যন্ত তার অনেকটাই মিথ্যা। পারিবারিক ও ব্যক্তিজীবনে, সম্পত্তির অধিকারে, ধর্মভিত্তিক ব্যবস্থাপনাকে স্বীকৃতি দিয়ে কিভাবে ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র গড়ে তোলা যায়, এ প্রশ্নটি না তুলে বরাবরই ‘বিসমিল্লাহ’ আছে কি নাই-এ বিতর্কের মধ্যেই ধর্মনিরপেক্ষতার ধারণাকে বিশ্লেষণ করার চেষ্টাকে আটকে রাখা হয়।
স্থানীয় সরকার ব্যবস্থা নিয়ে ইদানীং কিছু আলোচনা বিভিন্ন মহল থেকে তোলা হচ্ছে। তারা স্থানীয় সরকার ব্যবস্থার পক্ষে সংবিধানের মূলনীতি অধ্যায়ের ১১নং অনুচ্ছেদে বর্ণিত “প্রশাসনের সকল পর্যায়ে নির্বাচিত প্রতিনিধিদের মাধ্যমে জনগণের কার্যকর অংশগ্রহণ নিশ্চিত হইবে” অঙ্গীকারটির সাথে সংবিধানের নির্বাহী বিভাগের ৩য় পরিচ্ছেদে বর্ণিত “স্থানীয় শাসন” সংক্রান্ত ২টি অনুচ্ছেদ ৫৯ ও ৬০-কে উল্লেখ করে অনেকে দাবি করেন সংবিধান, “স্থানীয় শাসনের” পক্ষে স্পষ্ট অবস্থান নিয়েছে। আমাদের উচ্চ আদালতের এ বিষয়ে একাধিক রায়ও আছে। উপরোল্লিখিত তিনটি বিষয়কে মিলিয়ে পাঠ করলে যে কোনো পাঠক, সংবিধান সাধারণভাবে নির্বাচিত শক্তিশালী স্থানীয় শাসনের পক্ষে আছে এটাই দেখতে পাবেন। কিন্তু তারা যদি অনুচ্ছেদ ৫৯(২) পড়ার সময় “এই সংবিধান ও অন্য কোন আইন-সাপেক্ষে সংসদ আইনের দ্বারা যেরূপ নির্দিষ্ট করিবেন”, এই অংশটির উপর চোখ ফেলেন তাহলেই স্পষ্ট হয়ে যাবে নির্বাচিত “উপজেলা পরিষদ” কেন, কিভাবে ঠুঠু জগন্নাথে পরিণত হয়, অথবা কিভাবে “সিটি কর্পোরেশন”-এর নির্বাচিত মেয়রের বদলে সরকারি আমলারা কর্পোরেশনের প্রশাসক নিযুক্ত হয় এবং বহাল থাকে।
আইন প্রণয়নে সংসদের একচ্ছত্র ক্ষমতা নিয়ে ইতিপূর্বে যে আলোচনা হয়েছে তা অনেকটা বিভ্রান্তিকর হয়ে উঠবে যদি এ ক্ষেত্রে সরকারি আমলাদের ভুমিকা সম্পর্কে সামান্য অলোকপাতও না করা হয়। সংবিধানের বিবিধ অধ্যায়ে অনুচ্ছেদ ১৫২, যেখানে বিভিন্ন বিষয়ের সংজ্ঞা দেয়া হয়েছে সেখানে আইন বলতে কি বুঝাবে তাতে বলা হয়েছে: “আইন” অর্থ কোন আইন, অধ্যাদেশ, আদেশ, বিধি, প্রবিধান, উপ-আইন, বিজ্ঞপ্তি ও অন্যান্য আইনগত দলিল এবং বাংলাদেশে আইনের ক্ষমতাসম্পন্ন যে কোনো প্রথা বা রীতি। ঔপনেবেশিক ব্রিটিশ এবং পাকিস্তানি গণবিরোধী শাসনের যে আইনী কাঠামোর বিরুদ্ধে মানুষ দীর্ঘ লড়াই করেছে তার প্রায় সিংহভাগই ছিল আমলাতান্ত্রিকতা বিরোধী লড়াই। আমলাতান্ত্রিক এইসব আইন আমলাদের দ্বারা আমলাদের কর্তৃত্ব ও স্বার্থ রক্ষার জন্য সংবিধানের ফাঁক গলিয়ে তৈরি করা হতো। আমাদের সংবিধান প্রণেতারা সেই ফাঁককে এতটাই প্রসারিত করেছেন যে দেশ আমলাদের কৃত সেইসব আদেশ, বিধি, প্রবিধান, উপ-আইন আর বিজ্ঞপ্তির বাইরে এক মুুহূর্তও চলতে পারছে না। আমাদের একজন শিক্ষক তার একটি গবেষণায় এরকম ৩৪০০টি এস.আর.ও. নিয়ে গবেষণা করে দেখিয়েছেন কিভাবে আমলারা এখনো দেশের আইনের একটি বিশাল অংশকে নিয়ন্ত্রণ করে চলেছে। আর আমলাদের তৈরি এইসব আইনে দেশ চলে বলেই কখনো যথাযথভাবে আইন না মানার জন্য অথবা আইন ভঙ্গ করে ব্যক্তিগত ফায়দা হাসিলের অপরাধে তারা শাস্তি ভোগ করে না।
সংবিধান সংশোধনের শুরু ও তার রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট
নতুন সংবিধান তৈরির অল্প দিনের মধ্যেই সংবিধান সংশোধন প্রক্রিয়াও শুরু হয়। এই প্রক্রিয়াকে আলোচনার সুবিধার্থে কয়েকটি কালপর্বে ভাগ করা যায়:
(ক) একাত্তর থেকে পঁচাত্তর পর্ব; (খ) সামরিক শাসন পর্ব (১৯৯০ পর্যন্ত); (গ) নব্বই-পরবর্তী পর্ব।
১৯৭২ সালের ১৬ ডিসেম্বর থেকে আজ পর্যন্ত সংবিধানের সংশোধন হয়েছে পনেরোবার। এইসব সংশোধনীর কোনোটিই সংবিধানের যে অন্তর্নিহিত অগণতান্ত্রিকতা তা দূর করার উদ্যোগ নেয়নি। বেশিরভাগ ক্ষেত্রে এসব সংশোধনী আনা হয়েছে সংবিধানের মধ্যে যে আপাত গণতান্ত্রিকতার ছাপ ছিল তাকেও কলুষিত করে। জনগণকে আরো বেশি অধিকারহীন করার জন্য, পক্ষান্তরে জনগণের শাসক ও শোষকদের আরো বেশি শক্তিশালী করার জন্য। এক্ষেত্রে ক্ষুদ্র কিছু ব্যতিক্রমও রয়েছে; যেমন- প্রথম সংশোধনী।
১৯৭৩ সালের ২২ সেপ্টেম্বরে এই সংশোধনী পাস হয়। ’৭৩ সালের এই সংশোধনী মূল সংবিধান নাগরিকদের যতটুকু অধিকারকে মৌলিক অধিকার হিসাবে স্বীকৃতি দিয়েছিল তা থেকে স্পষ্টভাবে সরে আসে। মৌলিক অধিকার অধ্যায়ের ৩৩ নং অনুচ্ছেদে কাউকে বিনা বিচারে কারণ না জানিয়ে আটক না রাখার যে বিধান করা হয়েছিল তা থেকে রাষ্ট্রকে সরিয়ে আনা হয় এই সংশোধনীর মাধ্যমে। রাষ্ট্র এক্ষেত্রে বিদেশী শত্রু বা নিবর্তনমূলক আইনের অধীনে আটক (Preventive detention) ব্যক্তিদের বেলায় এ আইনের কার্যকারিতা বাতিল করে দেয়।
এ সংশোধনীতে সংবিধানে জরুরি অবস্থা ঘোষণার ব্যবস্থা সম্বলিত অনুচ্ছেদ ১৪১(ক) যুক্ত করা হয় এবং জরুরি অবস্থার কালে মৌলিক অধিকার রহিত করার বিধানসহ, সংবিধানের মৌলিক অধিকার পরিপন্থী আইন জারি করার ব্যবস্থা রাখা হয়। এভাবেই বাংলাদেশের নতুন সংবিধানে জনবিরোধী ফ্যাসিস্ট রাজনীতির শক্তিশালী ভিত্তি রচিত হতে শুরু করে।
দ্বিতীয় সংশোধনীটি Special Power’s Act-1974 জারি করার পথ শুধু উন্মুক্ত করেই ক্ষান্ত হয়নি, সংবিধানে ২৬(৩) ধারা যুক্ত করে বলে দেয় যে, সংবিধান সংশোধনের মাধ্যমে (অনুচ্ছেদ ১৪২-এর অধিকারবলে) যদি কোনো সংশোধনী আনা হয় তবে তা মৌলিক অধিকার পরিপন্থী হলেও বাতিলযোগ্য হবে না। অর্থাৎ এর মাধ্যমে সংবিধানে মৌলিক অধিকার পরিপন্থী আইন তৈরি করার রাস্তা করে দেয়া হয়।
তৃতীয় সংশোধনী
১৬ মে ১৯৭৪ সালে দিল্লিতে ভারতের প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী এবং বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ মুজিবুর রহমানের মধ্যকার সীমানা চুক্তিকে বাস্তবায়নের জন্য ২৮ নভেম্বর ১৯৭৫ সালে এই সংশোধনীটি পাস করা হয়। আঙ্গুরপোতা, দহগ্রাম, বেরুবাড়িসহ বিভিন্ন নদ-নদী, ছিটমহল এই চুক্তির অন্তর্ভুক্ত ছিল। উল্লেখ্য, ভারত আজ পর্যন্ত চুক্তির আলোকে তার সংবিধান সংশোধন করেনি, তাই তাদের পক্ষে চুক্তিও প্রতিপালিত হচ্ছে না।
চতুর্থ সংশোধনী
বাংলাদেশের সংবিধানের ইতিহাসে সবচাইতে ভয়াবহ সংশোধনীটি হলো চতুর্থ সংশোধনী। শেখ মুজিব রহমানের জীবদ্দশায়ই এটা ঘটে। ১৯৭৫ সালের ২৫ জানুয়ারিতে তৎকালীন জাতীয় সংসদ অতি অল্প সময়ে বিনাবিতর্কে সংশোধনীটি পাস করে।
এ সংশোধনীর মাধ্যমে দেশে সংসদীয় মন্ত্রী পরিষদ শাসিত সরকারের বদলে রাষ্ট্রপতি শাসিত সরকার ব্যবস্থা প্রবর্তিত হয়। মৌলিক অধিকার বলবৎকরণের জন্য হাইকোর্টের পরিবর্তে সাংবিধানিক আদালত বা কমিশন রাখার বিধান করা হয়। হাইকোর্ট-সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতি নিয়োগ এবং বরখাস্তের ক্ষমতা রাষ্ট্রপতির কাছে ন্যস্ত করা হয়। প্রশাসনের সকল স্তরে নির্বাচিত প্রতিনিধিদের মাধ্যমে জনগণের অংশগ্রহণের যে মূলনীতি ছিল, রাষ্ট্র তা বাতিল করে দেয়। রাষ্ট্রপতির অপসারণের জন্য, অপরাপর শর্তের সঙ্গে সংসদের তিন-চতুর্থাংশ সদস্যের ভোটে বিষয়টি পাস হওয়ার শর্ত যুক্ত করা হয়। সংবিধানের ৭০ অনুচ্ছেদ যেখানে সংসদ সদস্যের দলের বিরুদ্ধে ভোট দিলে সদস্যপদ বাতিল হওয়ার বিধান ছিল, তার ব্যাখ্যা যুক্ত করে বলা হয় যদি কোনো সদস্য উপস্থিত থেকে ভোটদানে বিরত থাকেন অথবা অনুপস্থিত থাকেন তাহলে তা-ও দলের বিপক্ষে ভোট দিয়েছেন বলে গণ্য হবে।
সংবিধানের ১০২ অনুচ্ছেদে থাকা হাইকোর্টের রিট ক্ষমতা খর্ব করা হয় এই সংশোধনীতে। সর্বোপরি সংবিধানে ‘ষষ্ঠ-ক ভাগ’ যুক্ত করে সকল রাজনৈতিক দল বন্ধ করে একটি রাজনৈতিক দল চালু করার ব্যবস্থা করা হয়। প্রজাতন্ত্রের কর্মে নিযুক্তদের জাতীয় দলে সদস্য হওয়ার ব্যবস্থা করা হয়। সংসদ সদস্যদের মধ্যে যারা জাতীয় দলে অন্তর্ভুক্ত হবে না তাদের সদস্যপদ শূন্য হওয়ার আইন করা হয়। জাতীয় দলের বাইরে অন্য কোনো দল গঠন বা কোনো রাজনৈতিক কর্মকান্ড পরিচালনা নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয় এবং এই সংশোধনী প্রবর্তনের পর হতে পরবর্তী পাঁচ বছরের জন্য বিদ্যমান সংসদকেই কার্যকর ঘোষণা করা হয়। সংবিধানে প্রথমবারের মতো শেখ মুজিবুর রহমানের নাম “জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান” হিসাবে উল্লেখ করা হয়। বিনা নির্বাচনে পরবর্তী পাঁচ বছরের জন্য শেখ মুজিবুর রহমানকে নির্বাচিত প্রেসিডেন্ট হিসাবে ঘোষণা করা হয়।
এই সংশোধনীর মধ্যে আরো কি কি করা হয়, তা বিস্তারিত আলোচনা করে দেখার জন্য অনেক বড় পরিসর প্রয়োজন। কিন্তু সবচাইতে গুরুত্বপূর্ণ যে বিষয়টি এখানে বিবেচনা করা দরকার তাহলো, এ সংশোধনীটি কিন্তু সংবিধান পরিবর্তনের জন্য ১৯৭২ সালের সংবিধানের দশম ভাগে ১৪২ নং অনুচ্ছেদ যে পথ বা পদ্ধতি নির্ধারণ করেছিল তা অনুসরণ করেই করা হয়।
এ থেকে একটি বিষয় সহজে অনুমান করা যায়, যারা (এখনও) ’৭২-এর সংবিধানকে একটি উৎকৃষ্ট গণতান্ত্রিক সংবিধান মনে করেন, তারা দুই-তৃতীয়াংশ সংসদ সদস্যের কাছে সংবিধানের যে কোনো পরিবর্তনের ক্ষমতা থাকাকে গণতন্ত্র মনে করেন, দেশের কোটি কোটি মানুষের মতামতকে নয়।
চতুর্থ সংশোধনীটি সংশোধনী হিসাবে কতটা অগণতান্ত্রিক, স্বৈরাচারী বা ফ্যাসিস্ট সেটা এ পর্যায়ে যতবড় বিবেচ্য বিষয়, তার চেয়েও বেশি বিবেচ্য হওয়া উচিত এটা যে, এই সংশোধনীটি না হলে বোঝা যেত না, ’৭২-এর সংবিধান কত বড় অগণতান্ত্রিক এবং ফ্যাসিবাদী হয়ে ওঠার আইনগত ক্ষমতা তার ভেতরে ধারণ করে ছিল বা আছে। এই সংবিধান যে কাঠামোগতভাবেই গণতন্ত্রবিরোধী এবং ক্ষেত্র বিশেষে দেশ-বিধ্বংসী উপাদান নিজের ভেতরে ধারণ করে আছে তা ‘জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান’ নিজেই উন্মোচিত করে দেখিয়েছিলেন।
এরপরের রাজনৈতিক ঘটনাবলি সবারই জানা। ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট এক মর্মান্তিক সামরিক অভ্যুত্থানের মাধ্যমে শেখ মুজিবুর রহমান এবং তার পরিবারের সদস্যদের হত্যা করা হয়। জারি করা হয় সামরিক আইন। ১৯৭১ থেকে ১৯৭৫-এর রাজনীতি বাংলাদেশের ইতিহাসের সবচাইতে টালমাটাল এবং অস্থিরতার রাজনীতি। সেসব নিয়ে বিশদ আলোচনার সুযোগ এখানে নাই এবং প্রয়োজনও নাই। তবে এটুকু আক্ষেপের সঙ্গে বলতে হয়, পাকিস্তানের জন্মলগ্ন থেকে বাংলাদেশের স্বাধীনতা পর্যন্ত যিনি অগ্রভাগে থেকে একটি গণতান্ত্রিক সংবিধানের জন্য লড়াই করেছেন, যার হাত ধরে একটি দেশ এবং সংবিধানের জন্ম হয়েছিল তার মৃত্যুর পূর্বেই তার স্বপ্নের গণতান্ত্রিক সংবিধানের মৃত্যু তার হাতেই সম্পন্ন হয়েছিল। আরো আক্ষেপের বিষয় হলো, শেখ মুজিবকে এ কাজে উৎসাহ ও সহযোগিতা দিয়ে গেছে অপেক্ষাকৃত প্রগতিশীল নামধারী কয়েকটি বামপন্থী রাজনৈতিক দল।
১৯৭৩ সালের ২২ সেপ্টেম্বরে এই সংশোধনী পাস হয়। ’৭৩ সালের এই সংশোধনী মূল সংবিধান নাগরিকদের যতটুকু অধিকারকে মৌলিক অধিকার হিসাবে স্বীকৃতি দিয়েছিল তা থেকে স্পষ্টভাবে সরে আসে। মৌলিক অধিকার অধ্যায়ের ৩৩ নং অনুচ্ছেদে কাউকে বিনা বিচারে কারণ না জানিয়ে আটক না রাখার যে বিধান করা হয়েছিল তা থেকে রাষ্ট্রকে সরিয়ে আনা হয় এই সংশোধনীর মাধ্যমে। রাষ্ট্র এক্ষেত্রে বিদেশী শত্রু বা নিবর্তনমূলক আইনের অধীনে আটক (Preventive detention) ব্যক্তিদের বেলায় এ আইনের কার্যকারিতা বাতিল করে দেয়।
এ সংশোধনীতে সংবিধানে জরুরি অবস্থা ঘোষণার ব্যবস্থা সম্বলিত অনুচ্ছেদ ১৪১(ক) যুক্ত করা হয় এবং জরুরি অবস্থার কালে মৌলিক অধিকার রহিত করার বিধানসহ, সংবিধানের মৌলিক অধিকার পরিপন্থী আইন জারি করার ব্যবস্থা রাখা হয়। এভাবেই বাংলাদেশের নতুন সংবিধানে জনবিরোধী ফ্যাসিস্ট রাজনীতির শক্তিশালী ভিত্তি রচিত হতে শুরু করে।
দ্বিতীয় সংশোধনীটি Special Power’s Act-1974 জারি করার পথ শুধু উন্মুক্ত করেই ক্ষান্ত হয়নি, সংবিধানে ২৬(৩) ধারা যুক্ত করে বলে দেয় যে, সংবিধান সংশোধনের মাধ্যমে (অনুচ্ছেদ ১৪২-এর অধিকারবলে) যদি কোনো সংশোধনী আনা হয় তবে তা মৌলিক অধিকার পরিপন্থী হলেও বাতিলযোগ্য হবে না। অর্থাৎ এর মাধ্যমে সংবিধানে মৌলিক অধিকার পরিপন্থী আইন তৈরি করার রাস্তা করে দেয়া হয়।
১৬ মে ১৯৭৪ সালে দিল্লিতে ভারতের প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী এবং বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ মুজিবুর রহমানের মধ্যকার সীমানা চুক্তিকে বাস্তবায়নের জন্য ২৮ নভেম্বর ১৯৭৫ সালে এই সংশোধনীটি পাস করা হয়। আঙ্গুরপোতা, দহগ্রাম, বেরুবাড়িসহ বিভিন্ন নদ-নদী, ছিটমহল এই চুক্তির অন্তর্ভুক্ত ছিল। উল্লেখ্য, ভারত আজ পর্যন্ত চুক্তির আলোকে তার সংবিধান সংশোধন করেনি, তাই তাদের পক্ষে চুক্তিও প্রতিপালিত হচ্ছে না।
বাংলাদেশের সংবিধানের ইতিহাসে সবচাইতে ভয়াবহ সংশোধনীটি হলো চতুর্থ সংশোধনী। শেখ মুজিব রহমানের জীবদ্দশায়ই এটা ঘটে। ১৯৭৫ সালের ২৫ জানুয়ারিতে তৎকালীন জাতীয় সংসদ অতি অল্প সময়ে বিনাবিতর্কে সংশোধনীটি পাস করে।
এ সংশোধনীর মাধ্যমে দেশে সংসদীয় মন্ত্রী পরিষদ শাসিত সরকারের বদলে রাষ্ট্রপতি শাসিত সরকার ব্যবস্থা প্রবর্তিত হয়। মৌলিক অধিকার বলবৎকরণের জন্য হাইকোর্টের পরিবর্তে সাংবিধানিক আদালত বা কমিশন রাখার বিধান করা হয়। হাইকোর্ট-সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতি নিয়োগ এবং বরখাস্তের ক্ষমতা রাষ্ট্রপতির কাছে ন্যস্ত করা হয়। প্রশাসনের সকল স্তরে নির্বাচিত প্রতিনিধিদের মাধ্যমে জনগণের অংশগ্রহণের যে মূলনীতি ছিল, রাষ্ট্র তা বাতিল করে দেয়। রাষ্ট্রপতির অপসারণের জন্য, অপরাপর শর্তের সঙ্গে সংসদের তিন-চতুর্থাংশ সদস্যের ভোটে বিষয়টি পাস হওয়ার শর্ত যুক্ত করা হয়। সংবিধানের ৭০ অনুচ্ছেদ যেখানে সংসদ সদস্যের দলের বিরুদ্ধে ভোট দিলে সদস্যপদ বাতিল হওয়ার বিধান ছিল, তার ব্যাখ্যা যুক্ত করে বলা হয় যদি কোনো সদস্য উপস্থিত থেকে ভোটদানে বিরত থাকেন অথবা অনুপস্থিত থাকেন তাহলে তা-ও দলের বিপক্ষে ভোট দিয়েছেন বলে গণ্য হবে।
সংবিধানের ১০২ অনুচ্ছেদে থাকা হাইকোর্টের রিট ক্ষমতা খর্ব করা হয় এই সংশোধনীতে। সর্বোপরি সংবিধানে ‘ষষ্ঠ-ক ভাগ’ যুক্ত করে সকল রাজনৈতিক দল বন্ধ করে একটি রাজনৈতিক দল চালু করার ব্যবস্থা করা হয়। প্রজাতন্ত্রের কর্মে নিযুক্তদের জাতীয় দলে সদস্য হওয়ার ব্যবস্থা করা হয়। সংসদ সদস্যদের মধ্যে যারা জাতীয় দলে অন্তর্ভুক্ত হবে না তাদের সদস্যপদ শূন্য হওয়ার আইন করা হয়। জাতীয় দলের বাইরে অন্য কোনো দল গঠন বা কোনো রাজনৈতিক কর্মকান্ড পরিচালনা নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয় এবং এই সংশোধনী প্রবর্তনের পর হতে পরবর্তী পাঁচ বছরের জন্য বিদ্যমান সংসদকেই কার্যকর ঘোষণা করা হয়। সংবিধানে প্রথমবারের মতো শেখ মুজিবুর রহমানের নাম “জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান” হিসাবে উল্লেখ করা হয়। বিনা নির্বাচনে পরবর্তী পাঁচ বছরের জন্য শেখ মুজিবুর রহমানকে নির্বাচিত প্রেসিডেন্ট হিসাবে ঘোষণা করা হয়।
এই সংশোধনীর মধ্যে আরো কি কি করা হয়, তা বিস্তারিত আলোচনা করে দেখার জন্য অনেক বড় পরিসর প্রয়োজন। কিন্তু সবচাইতে গুরুত্বপূর্ণ যে বিষয়টি এখানে বিবেচনা করা দরকার তাহলো, এ সংশোধনীটি কিন্তু সংবিধান পরিবর্তনের জন্য ১৯৭২ সালের সংবিধানের দশম ভাগে ১৪২ নং অনুচ্ছেদ যে পথ বা পদ্ধতি নির্ধারণ করেছিল তা অনুসরণ করেই করা হয়।
এ থেকে একটি বিষয় সহজে অনুমান করা যায়, যারা (এখনও) ’৭২-এর সংবিধানকে একটি উৎকৃষ্ট গণতান্ত্রিক সংবিধান মনে করেন, তারা দুই-তৃতীয়াংশ সংসদ সদস্যের কাছে সংবিধানের যে কোনো পরিবর্তনের ক্ষমতা থাকাকে গণতন্ত্র মনে করেন, দেশের কোটি কোটি মানুষের মতামতকে নয়।
চতুর্থ সংশোধনীটি সংশোধনী হিসাবে কতটা অগণতান্ত্রিক, স্বৈরাচারী বা ফ্যাসিস্ট সেটা এ পর্যায়ে যতবড় বিবেচ্য বিষয়, তার চেয়েও বেশি বিবেচ্য হওয়া উচিত এটা যে, এই সংশোধনীটি না হলে বোঝা যেত না, ’৭২-এর সংবিধান কত বড় অগণতান্ত্রিক এবং ফ্যাসিবাদী হয়ে ওঠার আইনগত ক্ষমতা তার ভেতরে ধারণ করে ছিল বা আছে। এই সংবিধান যে কাঠামোগতভাবেই গণতন্ত্রবিরোধী এবং ক্ষেত্র বিশেষে দেশ-বিধ্বংসী উপাদান নিজের ভেতরে ধারণ করে আছে তা ‘জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান’ নিজেই উন্মোচিত করে দেখিয়েছিলেন।
এরপরের রাজনৈতিক ঘটনাবলি সবারই জানা। ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট এক মর্মান্তিক সামরিক অভ্যুত্থানের মাধ্যমে শেখ মুজিবুর রহমান এবং তার পরিবারের সদস্যদের হত্যা করা হয়। জারি করা হয় সামরিক আইন। ১৯৭১ থেকে ১৯৭৫-এর রাজনীতি বাংলাদেশের ইতিহাসের সবচাইতে টালমাটাল এবং অস্থিরতার রাজনীতি। সেসব নিয়ে বিশদ আলোচনার সুযোগ এখানে নাই এবং প্রয়োজনও নাই। তবে এটুকু আক্ষেপের সঙ্গে বলতে হয়, পাকিস্তানের জন্মলগ্ন থেকে বাংলাদেশের স্বাধীনতা পর্যন্ত যিনি অগ্রভাগে থেকে একটি গণতান্ত্রিক সংবিধানের জন্য লড়াই করেছেন, যার হাত ধরে একটি দেশ এবং সংবিধানের জন্ম হয়েছিল তার মৃত্যুর পূর্বেই তার স্বপ্নের গণতান্ত্রিক সংবিধানের মৃত্যু তার হাতেই সম্পন্ন হয়েছিল। আরো আক্ষেপের বিষয় হলো, শেখ মুজিবকে এ কাজে উৎসাহ ও সহযোগিতা দিয়ে গেছে অপেক্ষাকৃত প্রগতিশীল নামধারী কয়েকটি বামপন্থী রাজনৈতিক দল।
১৯৭৯ সালের ৬ এপ্রিলে ৫ম সংশোধনীটি পাস হয়। এর রয়েছে একটি দীর্ঘ পটভূমি। এ সংশোধনীতে মূলত ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট হতে শুরু করে ১৯৭৯ সালের ৯ এপ্রিল পর্যন্ত সময়কালের মধ্যকার যাবতীয় ফরমান, আদেশ, ঘোষণা এবং ইত্যাদির দ্বারা কৃতকর্মসমূহকে বৈধ বলে ঘোষণা করা হয় এবং বলা হয় যে, এসব বিষয়ে কোনো আদালতে কোনো প্রশ্ন উত্থাপন করা যাবে না।
১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্টে শেখ মুজিবুর রহমানকে সপরিবারে হত্যার পর শেখ মুজিবের মন্ত্রীসভার সদস্য এবং আওয়ামী লীগের জ্যেষ্ঠ নেতা খন্দকার মোশতাক আহমদ সামরিক আইন জারি করেন। এ বিষয়ে প্রথম সামরিক ফরমানটি জারি হয় ২০ আগস্ট। এ ফরমানে তিনি নিজে সামরিক আইন জারির কথা ঘোষণা করেন। এভাবে একটি অদ্ভুত আইনের (যার কোনো অস্তিত্ব নাই বা ছিল না)-এর কথাও সংবিধানে প্রবিষ্ট হয়।
এ ঘোষণায় যদিও সংবিধানকে স্থগিত বা বাতিল করা হয়নি তবে সংবিধানের ৪৮, ৫৫ এবং ১৪৮ নং অনুচ্ছেদ, যেগুলো মূলত রাষ্ট্রপতি নির্বাচনের সঙ্গে সম্পর্কিত-সেই অনুচ্ছেদসমূহকে স্থগিত করেন। নিজেকে রাষ্ট্রপতি হিসাবে দাবি করে সুপ্রিম কোর্টসহ সকল আদালতকে মার্শাল ল’ রেগুলেশনের অধীনস্থ করার ঘোষণা দেন মোশতাক।
৮ নভেম্বর ১৯৭৫-এ এক ফরমান বলে তৎকালীন প্রধান বিচারপতি আবু সাদাত মোহাম্মদ সায়েমকে রাষ্ট্রপতি এবং প্রধান সামরিক আইন প্রশাসক, মেজর জেনারেল জিয়াউর রহমান এবং কমোডর এম. এইচ. খান এবং এয়ার ভাইস মার্শাল এম. এ. জি তোয়াবকে উপ-প্রধান সামরিক আইন প্রশাসক হিসাবে নিয়োগ করা হয়। নভেম্বর ৬ তারিখ থেকে সংসদ ভেঙ্গে দেয়া হয় এবং ১৯৭৭ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে সাধারণ নির্বাচন ঘোষণা করা হয়। ৪র্থ সংশোধনী বলে জারি করা সংবিধানের ৬ষ্ঠ ‘ক’ অধ্যায় (জাতীয় দল সংক্রান্ত) বাতিল ঘোষণা করা হয়। এভাবে বাকশাল অধ্যায়ের অবসান ঘটে। তবে এরপর একে একে সংবিধানে বহু কিছু পরিবর্তনের ধারাবাহিকতা চলে। যার প্রায় সবই ছিল তৎকালীন সামরিক শাসকদের বিবেচনা ও স্বার্থ তাড়িত। জনগণের মতামতের কোনো সুযোগ ছিল না তাতে।
৩১ ডিসেম্বর ১৯৭৫ সালে অপর এক ফরমান বলে সংবিধানের প্রথম তফসিল থেকে দালাল আইন ১৯৭২ (পি.ও. ৮/১৯৭২) বিলোপ (Omit) করে দেয়া হয়। এবং এর মধ্যদিয়ে ‘বাংলাদেশ’-এর বিরুদ্ধে আক্রমণকারীদের বিচার সম্ভাবনা শেষ হয়ে যায়। এর আগেই তাদের বিরাট সংখ্যকের জন্য সাধারণ ক্ষমাও ঘোষণা করা হয়।
১৪ মে ১৯৭৬ সালে অপর এক ফরমান বলে সংবিধানের ৩৮ অনুচ্ছেদে ধর্মীয় নামে রাজনৈতিক সংগঠন করার ওপর যে বাধানিষেধ ছিল সে অংশটি বাতিল করে দেয়া হয়। এভাবে বাংলাদেশে ধর্মভিত্তিক সাম্প্রদায়িক রাজনীতি চর্চার দ্বারও অবারিত হয়।
১৩ আগস্ট ১৯৭৬-এ সুপ্রিম কোর্ট এবং হাইকোর্ট আলাদা করা হয়। ২৮ জুলাই ১৯৭৬, রাজনৈতিক দল বিধিমালা-১৯৭৬ জারি করা হয় এবং ১৯৭৫-এর রাজনৈতিক দল নিষিদ্ধকরণ অধ্যাদেশ ও ১৯৬২ রাজনৈতিক দল আইন রহিত করে এক ফরমান জারি করা হয়। ২৬ নভেম্বর ১৯৭৬-এ এক ফরমান বলে জিয়াউর রহমানকে প্রধান সামরিক আইন প্রশাসক ঘোষণা করা হয়। ২৯ নভেম্বরে হাইকোর্টের ‘অন্তবর্তীকালীন’ আদেশ দেয়ার ক্ষমতা খর্ব করা হয়। এরফলে মানবাধিকার বিষয়ে উচ্চ আদালতের তরফ থেকে সাধারণ মানুষের স্বস্তিমূলক আদেশ পাওয়ার পথও সংকুচিত হয়ে যায়। ২১ এপ্রিল ১৯৭৭-এ বিচারপতি সায়েম নিজের শারীরিক অক্ষমতার কথা বলে জিয়াউর রহমানকে রাষ্ট্রপতি হিসাবে ঘোষণা করেন।
২৩ এপ্রিল ১৯৭৭-এ জিয়াউর রহমান রাষ্ট্রপতি এবং প্রধান সামরিক আইন প্রশাসক হিসাবে যে ফরমান জারি করেন তার মধ্যে প্রধান প্রধান দিক ছিল-তিনি সংবিধানে, প্রস্তাবনার ওপরে ‘বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম’; এবং প্রস্তাবনায়, ‘মুক্তির জন্য ঐতিহাসিক সংগ্রামের’ বদলে ‘জাতীয় স্বাধীনতার জন্য ঐতিহাসিক যুদ্ধের’ শব্দগুলো প্রতিস্থাপন করেন। এছাড়া প্রস্তাবনার দ্বিতীয় অনুচ্ছেদের বদলে ‘আল্লাহর উপর পূর্ণ আস্থা ও বিশ্বাস’ যোগ করা এবং মূলনীতি হিসাবে সমাজতন্ত্রের বদলে ‘সমাজতন্ত্র অর্থাৎ অর্থনৈতিক ও সামাজিক সুবিচার’ যোগ করে, ধর্মনিরপেক্ষতাকে বিদায় দেন।
একইভাবে রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতি অংশের অনুচ্ছেদসমূহকে পরিবর্তন করা হয়। মূলনীতি অংশের জাতীয়তাবাদ (অনুচ্ছেদ ৯) সমাজতন্ত্র (অনুচ্ছেদ ১০) ধর্মনিরপেক্ষতা (অনুচ্ছেদ ১২) বাতিল করে দেয়া হয়। আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে (অনুচ্ছেদ ২৫) ইসলামী রাষ্ট্রসমূহের সঙ্গে সম্পর্ক জোরদার করার ঘোষণা দেয়া হয়। যেখানে বিচারপতিদের অসদাচরণ কিংবা কর্তব্যে অবহেলার দরুণ অপসারণের ক্ষমতা রাষ্ট্রপতির হাতে নেয়া হয়েছিল (চতুর্থ সংশোধনী) তা বাতিল করে ‘জুডিশিয়াল কাউন্সিল’-এর রিপোর্ট ছাড়া কোনো বিচারপতিকে অপসারণ করা যাবে না বলে বিধান করা হয় এবং জুডিশিয়াল কাউন্সিলের গঠন কাঠামো নির্ধারণ করা হয়।
১ মে ১৯৭৭-তে জিয়াউর রহমান গণভোটের সিদ্ধান্ত ঘোষণা করেন। ৩০ মে ওই গণভোট অনুষ্ঠিত হয়। ১৯৭৮ সালের ৩ জুন, রাষ্ট্রপতি নির্বাচনের তারিখ নির্ধারণ করা হয় এবং জিয়াউর রহমান রাষ্ট্রপতি হিসাবে নির্বাচিত হন।
৬ এপ্রিল ১৯৭৯ সালে রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান সামরিক আইন প্রত্যাহার করেন এবং ৭ এপ্রিলে এই বিষয়ে একটি গেজেট প্রকাশিত হয়। উপরোক্ত সব সামরিক ফরমান, যার মাধ্যমে সামরিক আইন জারি বা প্রত্যাহার করা হয়েছে, যেখানে সংবিধানের মূলনীতি থেকে শুরু করে তফসিল পর্যন্ত পরিবর্তন করা হয়েছে, দালালদের বিচারের আওতা থেকে মুক্তি দিয়ে ধর্ম ব্যবহারকারীদের রাজনীতি ও সংগঠন করার অধিকার দেয়া হয়, নাগরিকত্ব থেকে জাতীয়তা সংক্রান্ত বিধান পরিবর্তন করা হয়, শেখ মুজিবুর রহমানের হত্যাকারীদের দায়মুক্তি দেয়া হয়-এরকম সকল ফরমানই বৈধ বলে সংবিধানে নতুন যে সংশোধনীটি আনা হয় তা হলো ৫ম সংশোধনী।
এখানে খুবই গুরুত্বের সঙ্গে আবারো লক্ষ্য করার বিষয় হলো, ’৭৫ সালে শেখ মুজিবুর রহমানকে সপরিবারে হত্যা করে সামরিক আইন জারি করা হয়েছে, কিন্তু সামরিক শাসকদের ক্ষমতা চর্চার পক্ষে ’৭২-এর সংবিধান বা আরো নির্দিষ্ট করে বললে, ’৭৫ সালের সংবিধান (৪র্থ সংশোধনীকৃত)-এর কোনো পরিবর্তন বা স্থগিত করতে হয়নি। অর্থাৎ ব্যক্তির ক্ষমতা চর্চার জন্য নানা দফায় সংবিধানে এত যে পরিবর্তন আনা হচ্ছে যা সামরিক একজন ব্যক্তির ক্ষমতা চর্চার পথে সংবিধান নিজে থেকে কোনো বাধা হয়ে দাঁড়ালো না। কারণ সংবিধানের মাঝে সেরকম কোনো সুরক্ষা ছিল না। কতিপয় অনুচ্ছেদ, যা রাষ্ট্রপতির নির্বাচন, শপথ, মেয়াদ ইত্যাদি সংক্রান্ত-সেরকম কয়েকটি অনুচ্ছেদ স্থগিত করার পরই তা সামরিক জান্তাদের ক্ষমতা চর্চার উপযোগী সংবিধানে পরিণত হয়ে যায়। জনগণকে নিপীড়নের হাত থেকে রক্ষার জন্য এ সংবিধান কখনো দাঁড়াতে পারেনি। ’৭২-এর সংবিধানের মধ্যে গণতন্ত্রকে ধ্বংস এবং লুণ্ঠনের যে অন্তর্নিহিত ক্ষমতা লুকায়িত আছে তাকে নিষ্ক্রিয় করার কোনো উদ্যোগ কেউই নেয়নি।
১৯৮১ সালের ৩০ মে এক সেনা অভ্যুত্থানে জেনারেল জিয়াউর রহমান নিহত হন। তার মৃত্যুতে উপ-রাষ্ট্রপতি বিচারপতি আব্দুস সাত্তারকে রাষ্ট্রপতি ঘোষণা করা হয় এবং উপ-রাষ্ট্রপতি রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হলে তার পদ যে শূন্য হবে এই ঘোষণার জন্য সংবিধান সংশোধনের প্রয়োজন দেখা দিলে ‘ষষ্ঠ সংশোধনী’ আনা হয় জুলাইয়ের ১০ তারিখে। এক ব্যক্তির প্রয়োজনে সংবিধান কতটা সংশোধিত হয়েছে তারও একটি দৃষ্টান্ত এটা। এরকম দৃষ্টান্ত আরো পাওয়া যাবে পরে।
জিয়াউর রহমানের মৃত্যুর পর, সাত্তার সরকার ‘ব্যর্থ’ এবং ‘দুর্নীতিগ্রস্ত’ এইসব অভিযোগ এনে তৎকালীন সেনাপ্রধান এইচ. এম. এরশাদ ’৮২ সালের ২৪ মার্চ পুনরায় সামরিক শাসন জারি করেন এবং তার পূর্বসুরি জিয়াউর রহমান যেভাবে ‘বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল’ গঠন করেছিলেন তারই অনুসরণে তিনি নতুন রাজনৈতিক দল ‘জাতীয় পার্টি’ গঠন করেন। তার রাজনীতি চর্চা শুরু হয়। এরশাদ অবশ্য ক্ষমতা দখলের অব্যবহিত পর পরই ছাত্রদের আন্দোলনের মুখে পড়েন।
এরশাদ দুটি উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন আনেন প্রশাসনে। প্রশাসনকে মানুষের দোড়গোড়ায় নিয়ে যাবার কথা বলে প্রশাসনের বিকেন্দ্রীকরণের জন্য উপজেলা পদ্ধতি প্রবর্তন করেন। ১৯৮৫ সালে উপজেলা পরিষদ গঠন করা হয় সরাসরি জনগণের ভোটে নির্বাচিত চেয়ারম্যানদের নিয়ে।
এই সপ্তম সংশোধনী জেনারেল এরশাদকে ও তার শাসনামলের সকল কার্যক্রমকে ‘বৈধতা’ দেয়ার জন্য আনা হয়েছিল।
এছাড়া সংবিধানের অষ্টম সংশোধনী আনেন তিনি। এ সংশোধনীতে তিনি জিয়াউর রহমানের পথ ধরে সংবিধানের আরো ইসলামীকরণের জন্য অনুচ্ছেদ ২-এর পরে ২(ক) যুক্ত করেন-যাতে রাষ্ট্রধর্ম হিসাবে ইসলামের কথা সংবিধানে প্রবিষ্ট হয়। এর বাইরে তিনি সুপ্রিম কোর্টের হাইকোর্ট ডিভিশনের ঢাকা ব্যতীত ৬টি নতুন বিভাগ স্থাপন করেন, যথাক্রমে কুমিল্লা, চট্টগ্রাম, বরিশাল, যশোর, রংপুর এবং সিলেট বিভাগে।
পরবর্তী সময়ে হাইকোর্টের এক রায়ে উক্ত সংশোধনীর শেষোক্ত অংশকে অবৈধ ঘোষণা করে, হাইকোর্টের সকল বেঞ্চকে ঢাকায় ফেরত আনা হয়। কিন্তু রাষ্ট্রধর্ম রয়ে যায় সকলের ধরা ছোঁয়ার ঊর্ধ্বে।
১১ জুলাই ১৯৮৯-তে সংবিধানে নবম সংশোধনী আনা হয়-এটি মূলত উপ-রাষ্ট্রপতি পদ সৃষ্টি করে রাষ্ট্রপতি পদের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ অবস্থান তৈরি করার জন্য করা হয়।
২৩ জুন ১৯৯০ এরশাদ শাসনামলের সর্বশেষ সংশোধনীটি পাস হয়। এই সংশোধনীতে মূলত নারীদের জন্য সংসদে ৩০টি সংরক্ষিত আসনের মেয়াদ পরবর্তী দশ বছরের জন্য বাড়ানো হয়। এটা ছিল সংবিধানের দশম সংশোধনী।
ইতিমধ্যে নানাপথ পরিক্রমায় সর্বদলীয় ছাত্র ঐক্য, তিন দলীয় জোট, শ্রমিক কর্মচারী ঐক্য পরিষদ, কৃষক-ক্ষেতমজুরদের ১৭ সংগঠন, সম্মিলিত সাংস্কৃতিক জোট, সম্মিলিত আইনজীবী পরিষদসহ প্রায় সকল রাজনৈতিক ও পেশাজীবী সংগঠনের আন্দোলনের মুখে ১৯৯০ সালের ৬ ডিসেম্বর এরশাদ সরকার পদত্যাগে বাধ্য হয়।
এইচ. এম. এরশাদের ক্ষমতা হস্তান্তর এবং পরবর্তী নির্বাচনকে নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে অনুষ্ঠানের জন্য তৎকালীন আন্দোলনকারী সংস্থাসমূহের মাঝে যে মতৈক্য তৈরি হয়েছিল তার সাংবিধানিক রূপায়ণের জন্য প্রচলিত ব্যবস্থার মধ্যে কিছু পরিবর্তন আনতে হয়, যার জন্য শেষ পর্যন্ত একটি সংশোধনী আনা হয় যা সংবিধানের একাদশ সংশোধনী হিসাবে খ্যাত। এই প্রক্রিয়ায় তৎকালীন তিন জোটের রূপরেখা অনুযায়ী তৎকালীন প্রধান বিচারপতি সাহাবুদ্দিন আহমদ প্রধান বিচারপতির পদে ইস্তফা দিয়ে প্রথমে এরশাদ কর্তৃক উপ-রাষ্ট্রপতি নিযুক্ত হন।
উপ-রাষ্ট্রপতি পদে তার যোগদানের পথ সুগম করার জন্য প্রথমে উপ-রাষ্ট্রপতি মওদুদ আহমেদকে পদত্যাগ করতে হয়েছিল। সাহাবুদ্দিন উপ-রাষ্ট্রপতি হওয়ার পর তার কাছে এরশাদ পদত্যাগপত্র জমা দিলে তিনি অস্থায়ী রাষ্ট্রপতির দায়িত্বভার গ্রহণ করেন এবং তার নেতৃত্বে একটি তত্ত¡াবধায়ক সরকারের অধীনে একটি জাতীয় সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। নির্বাচন শেষে সাহাবুদ্দিন আহমদকে প্রতিশ্রুতি মোতাবেক প্রধান বিচারপতি পদ ফেরত দেয়ার জন্য যে সংশোধনীটি আনা হয় তার ভূমিকার একটি ঐতিহাসিক গুরুত্ব রয়েছে যার অংশবিশেষ নিম্নরূপ:
“যেহেতু অবৈধ ও অগণতান্ত্রিক সরকার অপসারণ করিয়া একটি নির্দলীয় নিরপেক্ষ সরকারের অধীন সুষ্ঠু, অবাধ ও নিরপেক্ষ নির্বাচনের মাধ্যমে গণতন্ত্রকে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দেওয়ার লক্ষ্যে দেশব্যাপী দুর্বার গণ-আন্দোলনের মুখে তৎকালীন রাষ্ট্রপতি পদত্যাগের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিতে বাধ্য হন; এবং যেহেতু দলমত-নির্বিশেষে ছাত্র-কৃষক-শ্রমিক-কর্মচারী, পেশাজীবী সংগঠন, প্রধান রাজনৈতিক জোট ও দল ও সর্বস্তরের জনগণের ঐতিহাসিক বিজয়ের পর তিনটি প্রধান রাজনৈতিক জোট ও দল ও প্রধান বিচারপতি জনাব সাহাবুদ্দিন আহমদকে নির্দলীয় ও নিরপেক্ষ সরকারের প্রধান হিসাবে দায়িত্ব গ্রহণের আহ্বান জানান;... সেই হেতু সংবিধানের এই সংশোধনী...”।
বাংলাদেশের ৪০ বছরের ইতিহাসে এটিই একমাত্র সংশোধনী বা সাংবিধানিক দলিল যেখানে আন্দোলনকারী সংস্থাসমূহের কর্মকান্ড কে স্বীকৃতি দেয়া হয়েছে। ‘ছাত্র-কৃষক-শ্রমিক-কর্মচারী, পেশাজীবী সংগঠন, প্রধান রাজনৈতিক জোট ও দল ও সর্বস্তরের জনগণ’-এর ঐতিহাসিক বিজয়ের মতো প্রসঙ্গগুলো এই সংশোধনীতে ঠাঁই পেয়েছে।
অর্থাৎ এই প্রথম একটি সংশোধনী হচ্ছে জনগণের একটি অংশের ইচ্ছার অভিব্যক্তি হিসাবে এবং সংবিধানে তার উল্লেখ থাকছে। উপরন্তু এটিই একমাত্র সংশোধনী যেখানে রাষ্ট্র ক্ষমতা দখলকারীকে ‘অবৈধ’ বলা হয়েছে আর রাষ্ট্র ক্ষমতার জন্য আন্দোলনকারীদের ‘বৈধ’ বলে স্বীকৃতি দেয়া হয়েছে।
সকল ক্ষমতার একচ্ছত্র মালিকানা যখন প্রধানমন্ত্রীর
সংবিধানে একাদশ সংশোধনীর মাধ্যমে সাহাবুদ্দিন আহমদ পুনরায় প্রধান বিচারপতি পদে ফেরত যান। আর ১৮ সেপ্টেম্বর ১৯৯১ সালে ‘দ্বাদশ সংশোধনী’ পাস করে ৪র্থ সংশোধনীর মাধ্যমে বিদায় হওয়া মন্ত্রীপরিষদ শাসিত সরকার ব্যবস্থাকে ফেরত আনা হয়। সকল রাজনৈতিক দলই তখন এই সংশোধন প্রক্রিয়াকে স্বাগত জানিয়েছিল। এভাবে রাষ্ট্রপতির বদলে আবারো সকল ক্ষমতার মালিক বানানো হয় প্রধানমন্ত্রীকে। উপ-রাষ্ট্রপতি পদ বাতিল করা হয়। বাতিল করা হয় উপ-প্রধানমন্ত্রীর পদও। এই সংশোধনীর মাধ্যমে যদিও ‘রাষ্ট্রপতি শাসিত’ সরকারের বদলে বাংলাদেশ আবারো ‘মন্ত্রীপরিষদ শাসিত’ সরকার ব্যবস্থায় ফিরে আসে কিন্তু কার্যত তা হয়ে দাঁড়ায় প্রধানমন্ত্রী শাসিত সরকার। প্রধানমন্ত্রীর হাতে এই সংশোধনী একচ্ছত্র ক্ষমতা তুলে দেয়। স্পষ্টভাবে বললে, এটা এক ব্যক্তি শাসিত সরকারেরও এক নিকৃষ্ট রূপ উপহার দেয় দেশকে।
এ পর্যন্ত অনুষ্ঠিত নির্বাচনসমূহের মধ্যে ১৯৯০ সালে নির্বাচন সম্পর্কে অভিযোগ ছিল সবচেয়ে কম। ’৯০-এর নির্বাচনে বিজয়ী বিএনপি যাতে পুনরায় ক্ষমতায় ফেরত আসতে পারে সেভাবে প্রশাসন, বিচার বিভাগ, নির্বাচন কমিশন ইত্যাদিকে ঢেলে সাজানো হয়েছে অভিযোগ করে পরবর্তী নির্বাচনও ‘নির্দলীয় নিরপেক্ষ তত্ত্বাবধায়ক’ সরকারের অধীনে অনুষ্ঠানের দাবিতে আওয়ামী লীগ আন্দোলন করে এরপর।
১৫ ফেব্রুয়ারি ১৯৯৬-তে বিএনপি একদলীয় নির্বাচনের মাধ্যমে ক্ষমতায় ফেরত এলে আন্দোলন আরো তীব্র ও রক্তক্ষয়ী রূপ ধারণ করে। সেই প্রেক্ষাপটে ১৯৯৬ সালের ২৮ মার্চ সংবিধান সংশোধন করে ‘নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকার’ ব্যবস্থা চালু করা হয়। এটাই হলো ত্রয়োদশ সংশোধনী।
নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থায় তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রধান হিসাবে সুপ্রিম কোর্টের আপিল বিভাগের সর্বশেষ অবসর গ্রহণকারী বিচারপতি অথবা তাকে না পাওয়া গেলে বা তিনি রাজি না হলে একাদিক্রমে তার পূর্বসুরি বিচারপতিদের মধ্য থেকে প্রধান উপদেষ্টা নিয়োগের ব্যবস্থা রাখা হয়। তত্ত্বাবধায়ক সরকারের কাজ যদিও নির্দিষ্ট এবং মেয়াদও সেই কাজ অনুযায়ী অনুমেয় তবুও তা নির্দিষ্ট ছিল না। ১৯৯৬ থেকে তিনটি জাতীয় নির্বাচন সমালোচনাসহ তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনেই অনুষ্ঠিত হয়েছে।
সর্বশেষ ২০০৯ সালের নির্বাচন অবশ্য ব্যতিক্রম। উক্ত নির্বাচনের আগে প্রধান দুটি দল রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষে লিপ্ত হওয়ার প্রেক্ষিতে সেনাবাহিনীর প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে তত্ত্বাবধায়ক সরকার জরুরি আইনের অধীনে পরিচালিত হয়। দীর্ঘ দুই বছর তত্ত্বাবধায়ক সরকার
ক্ষমতায় থাকায় এ নিয়ে ব্যাপক সমালোচনা হয়। ইতিমধ্যে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের সাংবিধানিক বৈধতা নিয়ে জনৈক আইনজীবীর একটি রিট আবেদন যা হাইকোর্টে খারিজ হয়েছিলÑতা আপিলে মঞ্জুর হওয়ার পর পূর্ণাঙ্গ রায় বেরুনোর আগেই আওয়ামী লীগ তত্ত¡াবধায়ক ব্যবস্থা বাতিলসহ ’৭২-এর সংবিধান পুনঃপ্রতিষ্ঠার নামে সংবিধানের আরেকটি বৃহৎ সংশোধনী আনে, যা সংবিধানের পঞ্চদশ সংশোধনী নামে খ্যাত। যা নিয়ে বর্তমানে দেশের রাজনৈতিক অঙ্গন ক্রমশ বিপদসঙ্কুল হয়ে উঠছে।
পঞ্চদশ সংশোধনীর পূর্বে ২০০৪ সালের ১৭ মে সংবিধানে আরেকটি সংশোধনী (চতুর্দশ সংশোধনী) আনা হয়েছিল। উক্ত সংশোধনীতে নারীদের জন্য সংসদে ৪৫টি সংরক্ষিত আসন রাখার ব্যবস্থা করা হয়েছে।
যে পর্যায়ে এসে জাতীয় সাংবিধানিক সংকটগুলো আবার প্রকট হয়েছে
নবম জাতীয় সংসদ নির্বাচনে আওয়ামী লীগ এককভাবে দুই-তৃতীয়াংশের বেশি আসন নিয়ে সরকার গঠন করার পর থেকেই, সংবিধান পরিবর্তন করে ’৭২-এর সংবিধান পুনঃপ্রবর্তন করা হবে বা তত্ত¡াবধায়ক সরকার বাতিল করা হবে এমন সব গুঞ্জন ছিল। গুঞ্জনের পালে হাওয়া লাগে সুপ্রিম কোর্টের আপিল বিভাগে তড়িঘড়ি করে ত্রয়োদশ সংশোধনীকে (তত্ত্বাবধায়ক সরকারব্যবস্থা) অবৈধ ঘোষণা করে রায় দেয়ার পর (এর বাইরে ৫ম এবং ৭ম সংশোধনীকেও অবৈধ ঘোষণা করে উচ্চ আদালত)। পূর্ণাঙ্গ রায়টি দীর্ঘ সময় পর প্রকাশিত হয় এবং তার লিখন প্রক্রিয়াও ইতিমধ্যে বহু বিতর্কের জন্ম দিয়েছে। এই রায়ের দোহাই দিয়েই তত্ত্বাবধায়ক সরকারব্যবস্থা বাতিল ও অন্যান্য সংশোধনী-সহ পঞ্চদশ সংশোধনীটি সংসদ কর্তৃক প্রকাশিত হয়েছে ৩ জুলাই ২০১২-তে। যা সাধারণভাবে আইন মন্ত্রণালয় থেকে হওয়ার রীতি।
এ সংশোধনীতে যদিও শুরুতে বলা হয়েছে: ‘নিম্নবর্ণিত উদ্দেশ্য পুরণকল্পে’ সংশোধনীটি আনা হয়েছে-কিন্তু সংশোধনীর কোথাও কথিত সেই ‘উদ্দেশ্য’-কে খুঁজে পাওয়া যায় না। যাহোক, এ সংশোধনীটিকে বলা হচ্ছে ঐতিহাসিক এবং দাবি করা হচ্ছে এ সংশোধনীর মাধ্যমে জনগণকে তার ‘গণতান্ত্রিক’ অধিকার ফেরত দেয়া হয়েছে। কিন্তু দুর্ভাগ্যজনক সত্য হলো এই সংশোধনীর মাধ্যমে অনুচ্ছেদ ৭-এর পরে ৭(ক) যুক্ত করে বলা হচ্ছে:
“কোন ব্যক্তি শক্তি প্রদর্শন বা শক্তি প্রয়োগের মাধ্যমে বা অন্য কোন অসংবিধানিক পন্থায়- ক. এই সংবিধান বা ইহার কোন অনুচ্ছেদ রদ, রহিত বা বাতিল বা স্থগিত করিলে কিংবা উহা করিবার জন্য উদ্যোগ গ্রহণ বা ষড়যন্ত্র করিলে; কিংবা
খ. এই সংবিধান বা ইহার কোন বিধানের প্রতি নাগরিকের আস্থা, বিশ্বাস বা প্রত্যয় পরাহত করিলে কিংবা উহা করিবার জন্য উদ্যোগ গ্রহণ বা ষড়যন্ত্র করিলে-তাহার এই কার্য রাষ্ট্রদ্রোহিতা হইবে।
অতীতে আমরা দেখেছি আওয়ামী লীগ সংবিধানে চতুর্থ সংশোধনী এনে গণতন্ত্রের ভিত্তিমূলে তীব্র ঝাঁকুনি দিয়েছিল। কাকতালীয় কিংবা পরিকল্পিত যেভাবেই ঘটুক না কেন সংবিধানের পঞ্চদশ সংশোধনের মাধ্যমেও ‘গণতন্ত্র’ তীব্র এক ঝাঁকুনির মুখোমুখি। বরং এক্ষেত্রে ঝাঁকুনির তীব্রতা আরো বেশি এবং আরও সুদূরপ্রসারী হতে বাধ্য।
সংবিধানের ৪র্থ সংশোধনীতে একটি ছাড়া সকল রাজনৈতিক দল নিষিদ্ধ করা হয়েছিল, ৪টি পত্রিকা ছাড়া সকল দৈনিক পত্রিকা বাতিল করা হয়েছিল, হাইকোর্ট-সুপ্রিম কোর্টের ক্ষমতা কেড়ে নেয়া হয়েছিল কিন্তু সেখানেও এমন কোনো বিধান করা হয়নি যে, ঐসব কর্মকান্ড কে সমালোচনা করা যাবে না, কিংবা ঐসব বিধিবিধানের প্রতি কোনো নাগরিকের আস্থা, বিশ্বাস বা প্রত্যয় পরাহত করার উদ্যোগ গ্রহণ করলেই তাকে মৃত্যুদন্ডে দন্ডিত করা যাবে-যেমনটি করা হয়েছে পঞ্চদশ সংশোধনীতে। সেদিক থেকে বিবেচনা করলে আওয়ামী লীগের বর্তমান সংশোধনীটি অতীতের চাইতে একধাপ অগ্রসরই বলতে হবে।
এ সংশোধনী বলে ’৭২-এর সংবিধানের মূল প্রস্তাবনাকে ফেরত আনা হয়েছে। তাতে কথিত মূলনীতি ফেরত এসেছে, ধর্মনিরপেক্ষতা ফেরত এসেছে। তবে প্রস্তাবনার আগে জিয়াউর রহমানের যোগ করা ‘বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম’ অনুবাদ-সহ অক্ষুন্ন রয়েছে। অবশ্য অনুবাদের আর একটি সংস্করণ ‘পরম দয়াময় সৃষ্টিকর্তার নামে’ যুক্ত হয়েছে। পঞ্চদশ সংশোধনীতে এইচ. এম. এরশাদের ‘রাষ্ট্রধর্ম ইসলাম’ও অক্ষুন্ন আছে। তবে এরশাদ কথিত ‘অন্যান্য ধর্ম’-কে নির্দিষ্ট করে বলা হয়েছে ‘হিন্দু, বৌদ্ধ, খ্রিস্টান-সহ অন্যান্য ধর্ম।’ খালেদা জিয়ার আমলে সংশোধিত ‘রাষ্ট্রপতি আর প্রধানমন্ত্রীর প্রতিকৃতি’-র বদলে ‘জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের প্রতিকৃতি’-র আইন করা হয়েছে। নাগরিকত্বের ‘বাঙালি’-ত্ব ফেরত আনা হয়েছে। বলা হয়েছে, বাংলাদেশের জনগণ জাতি হিসাবে বাঙালি এবং নাগরিকগণ বাংলাদেশী বলে পরিচিত হবেন। সংবিধানের মূলনীতি অংশের অনুচ্ছেদ ৮, ৯ (জাতীয়তাবাদ), ১০ (সমাজতন্ত্র ও শোষণমুক্তি), ১২ (ধর্ম নিরপেক্ষতা ও ধর্মীয় স্বাধীনতা) ’৭২-এর চেহারায় ফেরত এসেছে।
১৮-ক নামে নতুনভাবে একটি বিষয় যুক্ত হয়েছে যেখানে পরিবেশ ও জীব-বৈচিত্র্য সংরক্ষণ ও উন্নয়নের কথা বলা হয়েছে এবং ২৩ ক-তে উপজাতি, ক্ষুদ্র জাতিসত্তা, নৃ-গোষ্ঠী ও সম্প্রদায়ের সংস্কৃতির সংরক্ষণ ও উন্নয়নের কথা বলা হয়েছে। মৌলিক অধিকার অধ্যায়ের অনুচ্ছেদ ৩৮, যেখানে রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে ধর্মীয় সংগঠন করার ওপর বিধিনিষেধ ছিল তা ফেরত এসেছে পরিবর্তিত আকারে। ’৭০ ফেরত এসেছে ৭২সালের সংবিধানের আকারে। নতুন আর সংযোজন কিছু নাই। তবে সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠানের সময় যা অনুচ্ছেদ ১২৩-এ উপধারা (৩)-এ ছিল তা ফেরত এসেছে ’৭২-এর মতোই। ’৭২ সালে ক্ষমতায় থেকে নির্বাচন করার যে বিধান সংবিধান জারি করেছিল তা-ই নতুনভাবে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করেছে আওয়ামী লীগ। অর্থাৎ ’৭২ সালেও সংবিধানে একই রকম বিধান ছিল যে, ক্ষমতায় থেকেই নির্বাচন করা যাবে। যারা সেইদিন এইরূপ বিধান করেছিলেন-তারাই পরে এইরূপ বিধানের বিরুদ্ধে সোচ্চার হন। পুরো বিষয়গুলো একবার চালু করা-একবার বাতিল করার ইচ্ছাপূরণ খেলার মতোই। সেই আলোকেই পঞ্চদশ সংশোধনীতে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ দিক হয়ে ওঠে ‘তত্ত্বাবধায়ক সরকার’ ব্যবস্থা বাতিল। এ ছাড়া সংবিধানের প্রস্তাবনা, মূলনীতি সহ অনেক অনুচ্ছেদ সংশোধনের অযোগ্য বা অপরিবর্তনীয় হিসেবে ঘোষণা করা হয়েছে। সংক্ষেপে এই হলো পঞ্চদশ সংশোধনী।
উপসংহারের পরিবর্তে
এক. বাংলাদেশ স্বাধীনতার মধ্যদিয়ে যে সংবিধানটি অর্জন করেছে, প্রাথমিকভাবে, তা ব্রিটিশ ব্যবস্থারই বিকশিত রূপ।
বর্তমানে আমরা আমাদের দেশে যেসব আইন চালু দেখি তার অধিকাংশই আক্ষরিক অর্থেই ব্রিটিশপ্রণীত। ১৯৩৫ সালের শাসনতান্ত্রিক কাঠামো, ইন্ডিপেনডেন্স অ্যাক্ট, ফৌজদারি বা দেওয়ানি আইন, বিচারব্যবস্থা, এর ধরন-ধারণ, দর্শন, ন্যায়বিচার সম্পর্কিত ধারণা সবই ব্রিটিশদের।
১৯৪৭ সালের স্বাধীনতার পর থেকে এ দেশের মানুষ এসব আইনের অন্তর্নিহিত দুর্বলতা, অগণতান্ত্রিক এককেন্দ্রিকতা, বৈপরীত্য এসবের বিরুদ্ধে দীর্ঘ লড়াই সংগ্রাম গড়ে তুলেছে এবং এক পর্যায়ে সশস্ত্র লড়াইয়ের মধ্যদিয়ে নতুন করে স্বাধীনতা অর্জন করেছে। কিন্তু দুর্ভাগ্যজনক সত্য হলো, এ দেশের মানুষ আইন বা সংবিধান প্রণয়নের ক্ষেত্রে স্বাধীন হতে পারেনি।
দুই. পাকিস্তানি রাষ্ট্র কাঠামোর মধ্যে বাংলার স্বায়ত্তশাসনের সঙ্গে সংগতিপূর্ণ একটি সংবিধান প্রণয়নের জন্য যারা ইয়াহিয়া খানের এল.এফ.ও’-র মধ্যে নির্বাচিত হয়েছিলেন, দেশ সশস্ত্র যুদ্ধের ভেতর দিয়ে স্বাধীনতা অর্জনের পরেও স্বাধীনতার জন্য যারা প্রত্যক্ষ লড়াইয়ে নিয়োজিত ছিলেন, তাদের বাদ রেখে, সেইসব এল.এফ.ও প্রতিনিধিদেরকেই স্বাধীন বাংলাদেশের জন্য সংবিধান প্রণয়নের দায়িত্ব দেয়া হয়েছিল।
তিন. সংবিধান প্রণয়নের জন্য যাদের দায়িত্ব প্রদান করা হয়েছিল, তাদের দলীয় আনুগত্য, তথা দলীয় প্রধানের নিরঙ্কুশ আধিপত্য নিশ্চিত করার জন্য গণপ্রতিনিধিত্ব (খারিজ) আদেশ জারি করা হয়েছিল, যাতে স্পষ্ট করে বলা ছিল, যদি দল কাউকে বহিষ্কার করে তবে তার ‘গণপ্রতিনিধিত্ব’ বাতিল হয়ে যাবে এবং এই বাতিলের বিরুদ্ধে কোনো আদালত কোনো ব্যবস্থা নিতে পারবে না।
চার. দলীয় প্রধানের বংশবদ, অন্ধ অনুগতদের দিয়ে স্বাধীন দেশের গণতান্ত্রিক সংবিধান প্রণয়নের চেষ্টার মধ্যেই নিহিত ছিল, চরম অগণতান্ত্রিকতার বীজ।
পাঁচ. মুক্তিযুদ্ধের আশা-আকাক্সক্ষার সঙ্গে সংগতিপূর্ণ একটি সংবিধান প্রণয়নের বদলে, একটি গণবিরোধী, এককেন্দ্রিক ক্ষমতা চর্চার সংবিধান প্রণয়ন করা হয়, যার সাধারণ অভিব্যক্তি হলো গণমুখী এবং প্রগতিশীল, কিন্তু যা প্রকৃতপক্ষে স্বৈরতান্ত্রিক এবং প্রতিক্রিয়াশীল।
ছয়. স্বাধীনতার অব্যবহিত পর একটি সংবিধান প্রণীত হয়, প্রচলিত আইনের সাপেক্ষে (পড়ুন ব্রিটিশ ও পাকিস্তানি আইনের সাপেক্ষে) কিন্তু, প্রচলিত আইনসমূহকে সংবিধান সাপেক্ষে যুগোপযোগী করার কোনো নীতি গ্রহণ করা হয়নি।
সাত. একটি জাতিগত নিপীড়নে পিষ্ট, গণহত্যার শিকার জাতি অন্যান্য জাতিসত্তার অস্তিত্বকে স্বীকার করতে কুণ্ঠিত থাকে।
আট. একটি দীর্ঘ সংগ্রাম ও সশস্ত্র লড়াইয়ের ভেতর দিয়ে গড়ে ওঠা দেশপ্রেমিক, মানবতাবাদী মুক্তিযোদ্ধাদের বাদ দিয়ে ঔপনিবেশিক সেনাবাহিনীর কাছে রাষ্ট্রের নিরাপত্তার দায়িত্ব তুলে দেয়া হয়।
নয়. ব্যক্তিজীবন, সম্পদের উত্তরাধিকার ইত্যাদি সকল ক্ষেত্রে ব্রিটিশ অনুসৃত বিভিন্ন ধর্মীয় আইন বহাল রেখে রাষ্ট্রের ধর্ম নিরপেক্ষতার বুলিবাগীশী করা হয়।
দশ. সম্পদের মালিকানার পুঁজিবাদী ব্যবস্থাকে সমাজতন্ত্রের মোড়কে বিকৃত উপস্থাপনার মাধ্যমে রাষ্ট্রীয় সম্পদ লুট-পাটের বৈধ ব্যবস্থা প্রণয়ন করা হয়।
১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধ যে আকাক্সক্ষা আর স্বপ্ন নিয়ে গড়ে উঠেছিল-যার স্বীকৃতি আছে সংবিধানের প্রস্তাবনায় এবং রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতিতে, যার ছায়া আছে মৌলিক অধিকার অধ্যায়ে, এবং যার মূলকথা হচ্ছে, ‘প্রজাতন্ত্রের সকল ক্ষমতার মালিক জনগণ’, প্রজাতন্ত্রের ‘উৎপাদন যন্ত্র, উৎপাদন ব্যবস্থা ও বণ্টন প্রণালীসমূহের মালিক, নিয়ন্ত্রক হইবেন জনগণ,’ প্রজাতন্ত্রের সেই মালিকানা প্রতিষ্ঠার পথে অন্তরায় যে বিধিবিধান, সেইসব অসংগতি ও সাংঘর্ষিক বিষয়গুলো দূর করে রাষ্ট্রের ওপর জনগণের মালিকানা প্রতিষ্ঠার সংবিধান প্রণয়ন করতে হবে। সে লক্ষ্যে প্রয়োজন ব্যাপক মিলিত ভাবনা ও তৎপরতা।